প্রজন্ম
আলমগীর রেজা চৌধুরী
দীপ্তি সাধারণ না। অসাধারণও না। অতিশয় লীলাবতী। তার আদিখ্যেতার সীমা নেই। আহ্লাদী ঢঙে কথা শুনলেই বলা যায় এ মেয়ে অনেক ঘেড়েল। কথা বাণে কাবু করতে আপনাকে এক মিনিটও সময় দেবে না। আর দেবে কেন? ও কি কারো ধার ধারে? চটাং কথা এমন মধুর করে বলবে যেন এই মাত্র চাঁদের দেশ থেকে ফিরেছে। তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। একটু পরে নভোযানে চড়ে ফিরে যেতে হবে। আপনিও বিশ্বাস করে সায় দিয়ে সব কিছু মেনে নেবেন। ঠিক তখন দীপ্তি বলবে, ‘প্রশান্ত দা, নিজেরা তো ভদ্রলোক না। পাড়ায় এক মহিলা এসেছেন, আর অমনি কাঙালের মতো হামলিয়ে পড়েছেন। সবে এসেছে, আপনাদের চেনাজানার সুযোগ হলো না। এরমধ্যে এত কিছু? মহল্লার বড় ভাই সেজে বসে আছেন!’ প্রশান্ত বাবু মাথা নিচু করে বলবে, ‘আমার ভুল হয়েছে, দীপ্তি। বুঝতে পারিনি।’ দীপ্তির এথেলেট হিসেবে খ্যাতি আছে। ইন্টার কলেজ সাইকেলিংয়ে স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত। বর্শানিক্ষেপে সেরা স্কোরার। প্রতিদিন ব্যায়ামের ট্রাউজার পরে জিমনেশিয়ামের দিকে সাইকেল চালিয়ে যায়। জুনিয়ররা চিৎকার করে ডাকে, ‘দীপ্তি দি। দীপ্তি দি।’
সিটি দিয়েছিল জসিম কাকার বড় ছেলে তাপস। দীপ্তি সাইকেল থামিয়ে বলল, ‘তাপস, আমার খারাপ লাগছে। তুই চালিয়ে নিয়ে ক্লাবে পৌঁছে দে।’ তাপস অতি উৎসাহী হয়ে দীপ্তিকে রডে বসিয়ে ঘোরের মধ্যে নিজ বাড়িতে চলে যায়। বারান্দায় দাঁড়ানো জসিম কাকা। সরাসরি তাঁর সামনে। দীপ্তি বলে, ‘চাচা, তাপস আমাকে সিটি দিয়েছে। আমি ইচ্ছা করলে থাপ্পর মারতে পারতাম। ভাবলাম আপনি তার পূজনীয় পিতা। আপনিই মারুন। একজন কন্যার অপমান তো সহজ কথা না।’ জসিম কাকা অনেকটা বাকরুদ্ধ। তেড়ে মারত গেল তাপসকে। তার আগেই দীপ্তি বাধসেজে সব কিছু ম্যানেজ করে বলল, ‘আজ কাকা মারতে চায়। কাল কিন্তু আমি মারব।’ ব্যাস্। তাপস এক্কেবারে সোজা। সারাক্ষণ ‘দিদি দিদি’ বলে ঘুরঘুর করে।

এই শহরে দীপ্তিকে সবাই চেনে। মায়াময় মুখ। ঢেউ খেলানো বাহারি চুলের ভক্ত অনেক তরুণ। মাঝারি হাইট। উজ্জল চোখে অন্যরকম দ্যুতি আছে। দীপ্তির বয়সী মেয়েদের কেউ তুই বলে না। আপনিও বলে না। দীপ্তিকে বলে। প্রচুর ফ্যান ওর। ঠিক এ সময়ই আত্মহত্যা করে দীপ্তি। শহরে সহস্র মমতা ছড়িয়ে যায়। কী দুঃখ তার? আত্মহননের মতো এরকম সিদ্ধান্ত তার সঠিক হয় নি। ট্রেনার মজিদ ভুঁইয়ার সঙ্গে ওর ছিনালি স্বভাব ছিল। না না না, লাভ রোডের ফাস্ট বোলার রফিক ভাইয়ের সঙ্গে কী যেন শুনেছিলাম! সব গুজব। আসল কথা হলো, দীপ্তির চোখ শেষ দিকে পাংশুটে হয়েছিল! আত্মহত্যার আগে দীপ্তি কিছুই লিখে যায় নি। দীপ্তি দরকার মনে করেনি। যেখানে বসবাস করবে না সেখানে জানিয়ে লাভ কী? এ জীবনের প্রতি ওর তেমন দায় নেই। নেবে কেন? সংসার তো ও রকম না। অনেক দায় এখানে। অযাচিত করুণা কিলবিল করে কান্নার জোরে ভাসতে ভাসতে বলল, এত ব্যাকুল কেন? ছোট্ট এ সময় ফাঁকি দেবে কেন? নিশ্চয়ই দীপ্তির কষ্ট আছে। যা তাকে আত্মহননে প্ররোচিত করেছে।
শহরে দীপ্তির আত্মহত্যা নিয়ে গসিপ ছড়াতে থাকে। স্থানীয় কাগজগুলোয় বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করে বিস্তর লেখালেখি হয়। কেন দীপ্তির মতো সম্ভাবনাময় প্রাণ অকালে ঝরে যাওয়া! অনুতাপের বহরে শহর তোলপাড় করা মানববন্ধনসহ শোকসভায় আলোচিত দীপ্তির খুঁটিনাটি জীবন কথা উঠে আসে। পরিতাপের শেষ নেই। শোককাতর শহরের মানুষ মেয়েটিকে মনে রাখতে চায়। যারা একসময় ওর স্পষ্ট কথা নিয়ে নানা কথা বলেছে, তারা আজ বলছে, ‘দীপ্তি সঠিক, আমরাই বেঠিক।’
না দীপ্তি সঠিক না। ও ভীরু। মেরুদণ্ডহীন। এতদিন ওর যা আস্ফালন তা ভড়ং। ওর কোনো শক্তি ছিল না। মনোজগতের পলাতক আসামি। নইলে এত অল্প বয়সে পৃথিবীর প্রতি এত বিতৃষ্ণা কেন? ও তো জীবনে কিছুই দেখেনি। জীবন কত বৈচিত্র আর বেদনার লীলাভূমি! বিচরণ করার সাহস থাকতে হয়। কাউকে বলতে হয়, জগত সংসার তোমার জন্য। দীপ্তি সে কথা বলে নি। বললে হনন ওর ধারেকাছে ঘেষতে পারত না। ক্ষুধায় কাতর জননীর ভূমিকায় ক্লান্ত হতে হয় নি। উজ্জল মুখ চোখের ভ্রু-ভঙ্গি জগৎ দোল খায়। তার জন্য আর্তনাদ, বুকজুড়ে কুটকুট করে কামড়ে দেয়। দীপ্তি হননের আগে কী ভেবেছিলে তুমি! কোনো গভীর ক্রোধ? কোনো প্রেমান্ধ যন্ত্রণা! শূন্যতার নভোমণ্ডলে একখণ্ড ধোঁয়াশা চাঁদ। তাহলে তুমি বাঁচতে চাইতে। এ রকম চাওয়া-পাওয়া মানুষকে বাঁচতে শেখায়। বয়স এতটুক! নীতি কথার বহরে সমাজ বদলে দেবে। তোর মতো পরাজিতরা কিছুই পরিবর্তন করে না। পেছন থেকে কাট মারে। অথর্ব। দীপ্তির পুরুষ্ঠ হাতে লোমশ উপস্থিতি প্রমাণ করে ওর কিউবিক হেয়ার যৌনগন্ধ কাম লুকিয়ে আছে। জাপটে ধরে কোনো তরুণকে বলেনি, ‘আমি ভেনাস।’ বোকা মেয়ে। এই আনন্দের জন্য মনুষ্য জন্ম। এত আয়োজন রেখে চলে যায় কেউ! ধ্যাত। ফজিল মেয়ে। থাপ্পর দিয়ে দাঁতের হালি ফেলে দেওয়া উচিত। লুনাটিক। মৃত্যুর হলোসেশন দেয়াল তৈরি করে দিয়েছে, অতিক্রম করতে পারেনি। মুরত বোঝা গেছে। অযথা এত হাউকাউ।
দীপ্তি হাউকাউ করতে বলেনি। ও তো পৃথিবীর কেউ না। মমতাহীন। মরবিড রাজকন্যে। উদাস চোখ দিয়ে প্রাচীরঘেরা বাড়ির অলিন্দে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখে। অনুতাপে দগ্ধ হৃদয় নিয়ে মুক্ত বিহঙ্গকূলের উড়াউড়ি দেখে। আহা! দুঃখি মেয়েটিকে ক্ষমা করে দাও। করুণাই ওর প্রাপ্য। আজ থেকে নয় মাস সতের দিন আগে দীপ্তি বলে, ‘মনিশংকর দা, আপনার তৃপ্তিকে বিয়ে করা ঠিক হয় নি। ও আপনার অবহেলার শিকার।’ তারপর থেকে তৃপ্তির প্রতি সীমাহীন আকর্ষণ জেগে উঠেছে মনি শংকর বাবুর। তৃপ্তি অনুগত নারীর মতো পেছনে ঘুরঘুর করতে থাকে। দীপ্তি, আমরা কৃতজ্ঞ। অসংলগ্ন পদচারণা মানুষকে স্বপ্নহীন করে দেয়। তোমার কোনো স্বপ্ন ছিল না! থাকতেও পারে। মানব জীবন কত পদের? ঘৃণা ধরে যায়! আনন্দের সাম্পানে পাল উঠিয়ে কেউ কি দীর্ঘলয়ে ডাকে নি? ইশারা দিলেই পারতে। কেমন হুমড়ি খেয়ে পড়ত। কুমারী বিনুনির প্যাঁচে পড়ে কত কাহিনী তৈরি হতো। বলত, ওরে বাবা! দীপ্তি! মাফ চাই। ওর বিশল্যকরণী দাওয়াই দরকার নেই। এমনেই ভালো আছি। তুমি বলতে পারো, দরকার নেই। ঠিক আছে। ধরে নিলাম ও খেলোয়াড় হিসেবে দুর্বল। ছলনার পাশা খেলার কুশলী কারিগর হতে পারলে ভালো হতো। জীবনের প্রতি মায়া জন্মাত। ব্যর্থ নায়িকা। প্রেমান্ধ নায়ক পাওনি। হইহই রইরই। দীপ্তি মনি, এই যে তোমাকে নিয়ে কথা! দরকার কী? তুমি কি আমাদের কেউ? এই শহরের মানুষ জানে, পলাতকা কুমারী দীপ্তি রানি শ্মশানের নিভন্ত আগুনের নিচে ছাই হয়ে আছে। ধূসর রঙ ছাই। ভূমিতে ছড়িয়ে দিলে ফসল ভালো হতো। তাও কেউ করেনি। পোস্টমর্টেমের পর পরিতোষ দা বলল, ‘ওকে ঘরে নিয়ে কি হবে?’ শব যাত্রার আগে ওকে স্নানও করানো হলো না। তোমরা এমন কেন দীপ্তি মনি? আমার কিন্তু ঘুষি মেরে পরিতোষ দা’র নাক ভেঙে দিতে ইচ্ছে হয়েছিল। বলে কী কুলাঙ্গার? জন্ম সহোদর। বোনটির প্রতি এমন মমতাহীন আচরণ কি ঠিক হয়েছে? তুমি বলতে পারো, ‘ঠিক হয়েছে। আমি তো নরকের বাসিন্দা। আমার দায় ওরা নেবে কেন?’ চিতায় তোলার আগে জুবলি রোডের জসিম কাকা একগুচ্ছ রজনীগন্ধা হাতে নিয়ে তার শুভ্র গোঁফ-দাড়ির অন্তরালে শোককাতরোক্তি নিয়ে বলল, ‘মা জননী, সুখে থাক।’ সৌম্যকান্ত বৃদ্ধের সঙ্গে কেউ শরিক হয় নি। না পরিতোষ দা’ না সুখেন কাকা। দীপ্তি আত্মহত্যা করেছে এটাই যেন তার অপরাধ। কারণ খোঁজার আগেই আমাদের দীপ্তি মনি ছাই হয়ে গেছে। চিতার দগ্ধ অনলের পাশে সহজিয়া গাইছে যারা, তারা তোমার ভাই-বন্ধু, পাড়া-প্রতিবেশী। খোল-করতালের দ্রিমিকি শব্দ ভেসে আসছে, ‘সুন্দর দুনিয়া থেকে একদিন চলে যেতে হবে, হায় সুন্দর দুনিয়া…’
শবের নিকট দুনিয়াদারির আখ্যান শুনিয়ে লাভ কী? দীপ্তি কি ফিরে আসবে? কেউ কি কোনোদিন ফিরে আসে? হায়! দুনিয়ার এত রূপ-রস-গন্ধ চিতার অনলে ছাই হওয়া দীপ্তি মনির নিকট প্রয়োজনহীন।
আত্মহত্যার আগের সন্ধ্যেবেলায় দীপ্তির সাইকেলের ঘণ্টাধ্বনি শুনে চমকে উঠে বকুল তলায় দাঁড়িয়েছিলাম। দীপ্তি কি কিছু বলতে এসেছে? ওর তো কোনো সময় লাগে না। সাইকেলের এক প্যাডেলে পা রেখে খুব অবাক তাকিয়ে থাকল কতক্ষণ। কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই সাইকেল চালিয়ে মঠের ওইদিকটায় হারিয়ে গেল। কিছুই বলল না। ওই সময় কিছু কথা মাথায় এসেছিল আমার। বলার সুযোগ ছিল না। দীপ্তির জন্য কিছু মমতা আমার হৃদয়ে জমা আছে। দীপ্তি কি বিশ্বাস করবে? ওর মতো দুরন্ত অকপট নারীর কাছে কিছুই গ্রহণযোগ্য নয়। আমার কথা বলা হয় নি দীপ্তিকে। দীপ্তিও কিছু বলেনি। শুধু ভোর বেলায় সারা শহর চাউর হয়, ‘দীপ্তি গলায় ফাঁস নিয়েছে।’
দীপ্তিকে আমার দেখতে ইচ্ছে হয় নি। চিতার আগুনে ছাই হওয়ার আগ পর্যন্ত ওর চেহারা মনে করতে চাইনি। বকুল তলায় সাইকেলের প্যাডেলে এক পা দেওয়া বাঁকাচোখে তাকানো আবছায়ায় যে ঝিলিক ছিল তা মনে রেখেছি। আর এ শহরের তাবত মনুষ্যকূল দীপ্তি মনি নামক একজন অভিমানি নারীর কোনো কিছুই মনে রাখতে চায় নি। কত বিচিত্র শাখা-প্রশাখা দীপ্তির উপস্থিতি অদৃশ্য হতে হতে এখন বিলীয়মান পাখির ঝাপটা শুনতে পায়। দীপ্তি এখন উপকথা, আতঙ্কিত এক নারীর নামাঙ্কিত সিলমোহর।
পাদটীকা
এতবছর পর দীপ্তি মনিকে নিয়ে একটি কবিতা লিখতে ইচ্ছে হলো। শত চেষ্টা করেও একটা পঙ্ক্তি খুঁজে পেলাম না। দীপ্তি আবারও অনাবিষ্কৃত থেকে যায়।

শ্যামলতার মৃত্যুশিথান
ইমতিয়ার শামীম
ফুলঝোর এইখানে এসে বাঁক নিয়েছে ইছামতির দিকে; না কি এ নদীকে অন্য কিছু বলে? এ নদীতে কি রিঠা মাছ পাওয়া যায়? প্রশ্ন করে না রিপন, আর চোখেও এমন কোনো চিহ্ন থাকে না। তবে মাথার মধ্যে প্রশ্নটা বারবার ঘুরপাক খেতে থাকে তার।
অনীল তখনও বলে চলেছে, ‘আমি তহন কী করি, বলেন? হাড়িভর্তি মাছ, শালার ডাকাইতগুলা পা দিয়া এমন লাত্থি দিল, সব তো চলতি ট্রেনের দরজা দিয়া বাইরে গিয়া পইড়ল। ট্রেন যাইতেছে, তা ধরেন হান্ড্রেড মাইল বেগে—’ বলে সে একটু থামে, মনে হয় তার মাথার মধ্যে তিন রাস্তার মোড়ে তিনদিক থেকে তিনটা ট্রাক এসে নিজেদের ইজ্জত সামলাতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। আর তাই কথাবার্তার গতিও একটু ঢিলেঢালা হয়—‘তা হান্ড্রেড মাইল বেগে গেলিই কী, আর ষাট মাইল বেগে গেলেই কী? প্যাসেজের মইধ্যে মাথার উপরে টিমটিম কইরা একটা বাত্তি জ্বলতেছে আর বাইরে ধরেন জিগার আঠার মতো—চেনেন তো জিগার আঠা?’—বলে সে রিপনের দিকে অনিশ্চিত চোখে তাকালে জবাব পায়, ‘চিনব না কেন? জিগা গাছের গা ফেটে বের হয়, না?’
‘হ—হ—’ সোৎসাহে সায় দিয়েও বিব্রত কণ্ঠে অনীল বলে, ‘না, মানে ভদ্রলোক হইলে মানুষ তো আবার এইসব চিনতে পারে না।’
ভদ্রলোক শব্দটার ওপর খানিকটা ভর দিয়ে ফের হালকা স্বরে বলতে থাকে, ‘তাই জিগাইলাম আরকি! … তে শোনেন, বাইরে তহন জিগার আঠার মতো আঠাইলা আন্ধার, হান্ড্রেডা মাইল বেগে সেই আন্ধারও দৌড় মাইরতেছে। ভালো কইরা কিছুই আর দেহার উপায় নাই। শালার এক হারামী কি কইরল, জানেন? বুকের কাছে এই যে এইখানটায় ছুড়ি ঠ্যাকায়া কয়, বাইর কর—বাইর কর কইতেছি। আমি আর কই কী, ভয়ে তো আত্মা উইড়া গ্যাছে, কোন কামে আইলাম রে বাপ, ক্যান আমার শখ হইল মাছ নিয়া গঞ্জে যাওয়ার! আর ধরেন, লোভে তো মরে জোলা—তা আমি তো জোলাও না! তাইলে আমার ক্যান লোভ হইল বেশি দামে মাছ বিক্রি করার? কাঁপতে কাঁপতে কইলাম, ট্যাকা তো নাই—গঞ্জে যাইতেছি, বিয়ানে মাছ বেচমু। হে শালায় ‘হারামজাদা’ কইয়াই আমার মাছভর্তি পাতিলে দিল লাত্থি। আর গড়াইতে গড়াইতে ট্রেনের দরোজা দিয়া আন্ধারের মধ্যে নুক্কি দিল। মাগুর-জিয়াল ভর্তি মাছের পাতিল, কোনডা যে কোনখানে গিয়া পইড়ল! সঠাৎ কইরা কী হইল জানেন? শালার ডাকাইত ‘ওরে মারে’ কইরা আমার বুকের পার থাইকা ছুরি সরায়া নিচের দিকে তাকাইল। চায়্যা দেহি, শিং মাছের কাটায় ব্যাটার পায়ের নিচ থাইকা রক্ত বারাইতেছে।’
রহস্যময় হাসিতে অনীলের মুখ ভরে ওঠে। একটা মাঝারি ঢেউ এসে নৌকার তলায় ধাক্কা মারে। নৌকাটা দুলে দুলে ওঠে। আকাশ আজ ভীষণ পরিষ্কার, পুতুল আর হাতির বাচ্চা থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ কিংবা কার্ল মার্কস সবাই শাদা শাদা মেঘ হয়ে ভাসছে সেখানটাতে। হাসতে হাসতে অনীল বোধহয় তার গল্পের ইতি টানে, ‘আল্লায়ই বিচার করে।’
কথাটা খট করে কানে লাগে, তা হলে হিন্দু জেলে নয়!? কিন্তু নৌকা ছাড়ার আগে যেভাবে ভগবান বন্দনা করল, তাতে তো এরকমই ভেবেছিল সে। তবে এইসব তো জিজ্ঞেস করা যায় না। আর জিজ্ঞেস করার দরকারও নেই তার। ঠাঁ ঠাঁ দুপুরে একটা নৌকা পেয়েছে, এই তার সাত জন্মের ভাগ্য। দূরে রেলব্রিজটা ক্রমশই ছোট হয়ে আসছে। আর তার ওপর দিয়ে আবারও একটা ধাবমান ট্রেন আরো ছোট হয়ে যাচ্ছে।
এ তো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, এই এলাকায় যাতায়াতের পথ একটাই—রেলপথ; আর ট্রেন থেকে নামার পর সম্বল পা দুইখানা। ফাঁকফোকড়ে নৌকা, না হয় সাইকেল কিংবা গরুর গাড়ি—এর চেয়ে দ্রুতগামী কিছু আর নেই। স্টেশন থেকে নামার পর তাই তাকে হাঁটতেই হয়েছে। স্টেশনের বাইরে কয়েকটা গরুর গাড়ি ছিল। তবে কাপড়ের গাইট নিয়ে সেগুলো যাবে সেই এনায়েতপুরের দিকে। আর কাপড়বাহী মালগাড়ি কখন আসবে কেউ জানে না। তা ছাড়া ঠিক সময়ে এলেও তার ভাত ছিল না; একেকটা গরুর গাড়িতে গাড়োয়ান আর ছোট গাড়োয়ান ছাড়াও আছে কাপড়ের পার্টির একজন। এরা চড়ার পর তার আর বসার জায়গা কোথায়। তাও না হয় কথা বলে দেখা যেত; কিন্তু রিপনের মনে হচ্ছিল, অন্তহীন রোদের প্রেক্ষাপটে কয়েকটা গাছের নিচে রাখা গরুর গাড়িগুলো যেন একেকটা নিঃসঙ্গ কফিন, গরুগুলো তার আশপাশে দাঁড়িয়ে-বসে কোথায় কতটুকু সবুজ ঘাস আছে তা সাবাড় করার। সে হনহনিয়ে হাঁটতে শুরু করেছিল মেঠো সড়ক দিয়ে।
‘কই যাইবেন ভাই?’—কারো এই প্রশ্ন শুনে সে চমকে উঠেছিল। কোনো ভরাট কণ্ঠ নয়, কণ্ঠে কোনো সন্দেহ নেই, খুব বেশি আগ্রহ যে আছে, সেরকমও নয়। কিন্তু কিছু একটা তো নিশ্চয়ই ছিল। না হলে সে চমকে উঠবে কেন? আর চমকে উঠে সে মাথার ছাতিটা নামিয়ে ফেলবে কেন?
‘না—মানে আপনেক এ এলাকার মনে হয় না তো! তাই কইলাম।’
এতক্ষণে লোকটার অবস্থান ঠিকমতো বুঝতে পারে রিপন। আমগাছটার একটা ডাল বেশ নিচের দিকে; তার ওপরেই শুয়ে আছে লোকটা। আরো একজন আছে, তবে আরো একটু ওপরে। তা ছাড়া শোয়ার মতো দীর্ঘ ডাল পায়নি সে। গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে ডালে পাছা ঠেকিয়ে পা মেলে বসে আছে সে।
‘জ্বি, ভাই। আমি নতুন মানুষ। সোনতলা যাব।’
‘সে আপনেক দেখলিই বোঝা যায়। প্যান্টপরা মানুষ, লম্বা হাতার জামা। আবার হাতে ছোটখাটো ব্যাগও আছে একখান—’
লোকটা তার ব্যাগটাকে বারবার লোভী চোখে তাকাচ্ছিল। রিপন বুঝতে পারছিল না এর পর কী বলা যায়। বোকার মতো বলেছিল, ‘শুনছি, স্টেশন থেকে নেমে একটাই রাস্তা—সেই রাস্তা ধরে যেতে হবে, স্কুলটাও নাকি রাস্তার ধারে; তাই আর কাউকে জিজ্ঞেস করি নি।’
‘স্কুলে যাইবেন? মাস্টার হইবেন? বেতন পাইবেন না কইল।’
অদ্ভুত ব্যাপার! মনে হচ্ছে, স্কুলে পৌঁছানোর আগেই তার ইন্টারভিউ শুরু হয়ে গেছে। অথবা এমনও হতে পারে, স্কুলটার উদ্যোক্তাদের শত্রু অনেক—বাগড়া বসানোর মানুষজন সবখানে বসে আছে। সে মুখটা নিচু করে আবারও ছাতা খোলার প্রস্তুতি নিয়েছিল। আর তখন চোখটা স্টেশনঘরে আটকে গিয়েছিল। বিবর্ণ লাল রঙের ঘর, ছোট জানালায় কবে যে হালকা বার্নিশ করা হয়েছিল, কেউ জানে না। মোটা মোটা গোল শিকগুলোর ফাঁক দিয়ে স্টেশন মাস্টারকে দেখা যাচ্ছে বিরাট একটা খাতায় চোখ বুলাতে।
ছাতাটা খুলে মাথার ওপর নিয়ে রিপন হাসবার চেষ্টা করেছিল, ‘দেখি, যাই তো আগে—তার পর দেখি, কথা বলি…’
‘কথা কওয়ার কিছু নাই—’ ওপরের ডালের লোকটা বলেছিল— ‘আমরা সবই জানি। লজিং—লজিং থাকা লাইগব। বাগচী বাড়িত থাইকতে পারেন। খাইবেন দাইবেন, স্কুলে পড়াইবেন—বাগচী বাড়িত আইসা আবারও পড়াইবেন, বিধবা একটা মেয়ে আছে বাগচীর, একটা কচিও আছে। কচি, তবে বড়ই সরেস। বাগচী বাড়িত উঠলি আপনের প্যাট-চ্যাটের কুনু অভাব থাইকপো না—’
রিপনের কান গরম হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এই অজানা, অচেনা জনহীন প্রান্তরে সে কী আর করতে পারে! এইসব বলার পর লোকগুলোর হো হো করে হাসার কথা—কিন্তু সে কোনো হাসির শব্দ শোনা দূরে থাক, হাসির আভাস ফুটে উঠতেও দেখেনি লোকগুলোর ঠোঁটের কোণে। তবে কী যেন ছিল; এখন এই নদীর জলের দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পারে করুণ শুষ্ক জলের মতো কোনো কিছু।
নিচের ডালে শুয়ে থাকা লোকটা ফের চোখ বোজার আগে বলেছিল তাকে—‘মাঝখানে কইল নদী আছে একটা। নৌকা কইরা যাইয়েন। কষ্ট কম হইব।’
‘নৌকায় যাওয়া যায়?’
‘যায় তো। নৌকায় ঘাট পার হইয়া হাঁইটাও যাইতে পারেন—তাতে কষ্ট হইব আরকি। নৌকায় যাইবেন, সময় একটু বেশি লাইগব। আরামে যাইবেন, বাতাস খাইবেন—এই আরকি।’
আরো খানিকক্ষণ পরে রিপন এই নদী পেয়েছিল। তার শুকনো বুকে যেটুকু পানি আছে, তাও এখন সাঁতরে পেরুনো কঠিন। তবে ঘাটে কোনো নৌকা নেই; আর ইজারা নিশ্চয়ই এইবার ঘাটের ওই পাড়ের লোকজন পেয়েছে—ইজারাদারের টংঘরটা দেখা যাচ্ছে নদীর ওই পাড়ে। সে এইসব ভাবছে আর আশপাশ দেখছে; ঠিক তখনই ঝাঁপি ফেলা ঘরটার সামনে থেকে একটা কুকুর প্রচণ্ড বিরক্তি নিয়ে উঠে দৌড়াতে শুরু করেছিল দূরের বাড়িঘরগুলোর দিকে। রিপন শিউরে উঠেছিল। খরখরে এই দিনে, এই প্রান্তরে তার যে একেবারে খারাপ লাগছে, সেরকম না। হ্যাঁ, গরম পড়েছে বটে; কিন্তু গ্রীষ্মে তো গরমই থাকে। আর গরমকালে সে গরমই চায়, চায় প্রকৃতির শরীরের আস্বাদ নিতে। সে যদি সিনেমা বানাতে জানত, এই আদিগন্ত বিস্তৃত ল্যান্ডস্কেপটাকে নিশ্চয়ই ধরত; এই দুপুর, এই রোদ, নিঃসঙ্গ আর মরমরে গাছ-ঘাসগুলোর সালোক সংশ্লেষণ, দূরে ক্ষেতের মধ্যে মাথালপরা কৃষক, নদীর ওপারের বটগাছ আর এ পারের এই কয়েকটা জেলে নৌকা…
তরতরিয়ে গড়ান বেয়ে নিচের দিকে নেমে এসেছিল রিপন। তার কালো, পুরানো স্যান্ডেল স্যুটা হয়তো আর একটু এদিকসেদিক হলেই ছিঁড়ে যেত। কিন্তু সেদিকে নজর না দিয়ে সে সোজা জেলে নৌকাগুলোর দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। আর এইভাবে অনীলকে সে খুঁজে পেয়েছিল।
কিন্তু অনীল বড় বেশি কথা বলে। স্কুলের নামের অর্ধেক শুনেই সে হড়বড়িয়ে বলে উঠেছিল, ‘চিনি তো—আমার বাড়ির পাশেই তো। যাইবেন সেহানে? এই বিনয়, আমার জালটারে দেহিস তো। আমি ওনারে নামায়া দিয়া আসি।’
‘ভাড়া কত নেবেন?’—নৌকায় চড়ার আগেই রিপন জানতে চেয়েছিল। অনেকবার ঠেকে এইটা শিখেছে, ভাড়া-মজুরি ঠিক করে নিতে হয় কাজ শুরু করার আগেই। কিন্তু অনীল অবাক হয়ে বলেছিল, ‘ভাড়া? ভাড়া কিসের? আমাগারে গাঁয়ের স্কুলে যাইবেন, তার জইন্যে ভাড়া নিব আমি?’
নদীর জল স্থির ও স্থবির হয়ে আছে। এই সময়ে কেউ মাছ ধরে না। কিন্তু অভ্যাসবশে জেলেরা জাল ফেলে রেখেছে। মন্থর ঢিলে তালে দুই জেলে জাল তুলতে শুরু করলে অবাক চোখে রিপন দেখেছিল, অসংখ্য খুলি জালের মধ্যে খলবল করছে। ভয় আর বিস্ময়ে তার চোখমুখ নীল হতে হতেও লালচে-ফর্সা হয়ে গিয়েছিল। অনীল খুশিভরা গলায় বলেছিল, ‘এবার এই ম্যান্দামারা সময়েও কত মাছ ধরা পড়ছে, দেখেন—। বিনয় রে, মাস্টার সাবের জইন্যে এক খালই মাছ দে দেহি।’
খালইভর্তি মাছ নিয়ে অনীল তাকে নিয়ে চলেছে স্কুলের দিকে। কিন্তু কোনখানে স্কুল! সামনে অনন্ত জলপ্রান্তর, দিগন্তরেখার সঙ্গে মিশে আছে গাছপালা-বাড়িঘর। থির হয়ে আছে জল। এ সময় নদীর পানিতে কোনো স্রোতও থাকে না। ঠিক তার জীবনের মতো; এই তুলনাটা আসতে না আসতেই কেমন যেন কেঁপে ওঠে একেবারে ভেতর থেকে। স্রোতহীন নদীতে তবু কত রুপালি ছোট ছোট ঢেউ এত দ্রুত চলাচল করছে যে সহজেই চোখে আটকায় না। অনীল চলেছে অনেকটা কিনার ঘেঁষে, সেখানে মাঝেমধ্যে দলছুট কচুরিপাণা সবুজ জীবনের আভা ছড়াচ্ছে।
‘আপনে মাছ খান তো? কোন মাছ আপনের বেশি পছন্দের?’
কী সব আবোলতাবোল প্যাঁচাল জুড়েছে! এবার আর কথার উত্তর দিতে রিপনের ভালো লাগে না। কিন্তু একটা লোক ফাও ফাও তাকে নিয়ে যাচ্ছে এত পরিশ্রম করে, বিরক্তই বা সে হয় কেমন করে। কিন্তু উত্তর দেয়ার দরকার হয় না তার, আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে অনীল আবারও বলতে থাকে, ‘মাছের রাজা ইলিশ, এইটা কিন্তু ভুয়া কথা, বুইঝলেন? ইলিশ মাছ হইল ধরেন ওই ফিরনির মতো, খাইতে খুবই স্বাদের, কিন্তু আত্মা জুড়ায় না। কত মাছ যে আছে নদীর জলে! এক্কেরে ধরেন দিল্লীর মতো। দিল্লী টাউনে যেব্যা হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, ইহুদি, সাঁওতাল, জোলা, জাইলা, নমঃশুদ্র সব কিছিমের মানুষ ঘোরাফেরা করে, নদী হইল তাই। নদী হইল মাছগারে দিল্লী টাউন—’
‘আপনি দিল্লী গেছেন?’—আচমকা কী ভেবে বলে বসে রিপন।
‘আমি?…দিল্লী?…হেহ্, আমার কি আর হেই কপাল আছে? আমার দাদার পোলা ভীষণ ট্যাটন। কয় যে—’বলেই কী এক সংশয় নিয়ে হালের ওপর হাতটা স্থির করে ধরে অনীল তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর বলেই ফেলে, ‘কয় যে, কাকা, এই দ্যাশে থাকা যাইব না, ও তোমরা মুজিবেক যতই ভালোবাসো না ক্যান, তোমাগারে নৌকার লোকজন নৌকায় কইর্যা ভাসায়া দিব। আমার নাওয়ে ভাসার হাউস নাই, আমি দিল্লী গ্যালাম। হে চইল্যা গেছে। জাইলার পোলা ড্রাইভার হইছে। এই জন্যেই তো কই, দিল্লী হইল দুনিয়ার ব্যাবাক মানুষের জায়গা।’
‘কথাটা ঠিক না। লন্ডন—লন্ডন হলো সব রকম মানুষের জায়গা।’
অনীল বেকুবের মতো তাকিয়ে থাকে। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, ‘হইতে পারে। কথা তো ওইখানে না—কথা হইল, নদী হইল ব্যাবাক মাছগারে জায়গা। একটা মাছ আছে বুইঝলেন, নাম খসুল বাটা মাছ। খাইছেন কুনুদিন?’
নাহ্, এরকম কোনো মাছ খায়নি রিপন। শুধু খাওয়া কেন, এরকম কোনো মাছের নামও জানে না সে। তার জ্ঞানের ভাণ্ডার প্রায় শূন্য, আর মৎস্যের ভাণ্ডার নেই বললেই চলে। তাই মাথা নেড়ে না করতে না করতেই বলে ওঠে অনীল, ‘তাইলে দাদা, আজই চলেন, মাস্টার সাবের সাথে কাজকাম সাইরা আইজক্যাই চলেন রওনা হই করতোয়া, নয় তো বড়াল ব্রিজের দিকে।’
এবার একটু দুলুনি লাগে আর রিপন তার ব্যাগটা শক্ত করে চেপে ধরে। অনীল এবার হাল ছেড়ে লগি হাতে নিল। অগভীর নদীর বুকে লগিটা বারবার গেঁথে যাচ্ছে। তীরের এখানটায় এত বেশি গাছ যে মনে হয় বন। কিন্তু পায়ের চলার পরিষ্কার রাস্তা চলে গেছে গাছের ভেতর দিয়ে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় রিপন। কিন্তু অনীলের মুখ এখন বন্ধ আছে। ভীষণ ব্যস্ত সে শেষ মুহূর্তে নৌকাটাকে বাগে রাখতে। এখন দুলছেও বেশ। নৌকা ঘাটে ভেড়ার আগে এরকম হয়। তাই রিপন শান্ত থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে বেশ দমে যায় সে। এরকম একটা অজ পাড়াগাঁয়ে চাকরি করবে সে!
‘আসেন।’—বলে এবার অনীল তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে নৌকার গলুইয়ে দাঁড়ায়। নদীর তীরঘেঁষা অল্প পানির মধ্যে লগিটাকে গাঁথে ভালো করে। তারপর সেটার সঙ্গে নৌকাকে বেঁধে এদিকসেদিক দেখে নিয়ে হাতটা এগিয়ে দেয়, ‘ধরেন, লাফ দ্যান ইট্টু। কিনারে পা রাইখেন না, পিছলা যাইবেন।’
রিপন অনীলের বাড়িয়ে দেওয়া হাতটা ধরে লাফ দিয়ে যতদূর সম্ভব দূরে নামে। ডান হাত দিয়ে ব্যাগটাকে তখনও সে বুকে ধরে রেখেছে। আবারও জিজ্ঞাসু চোখে সে অনীলের দিকে তাকিয়ে থাকে। অনীল কেমন রহস্যময় হাসি দেয়, ‘আসেন আসেন’, ঢালু বেয়ে সে ওপরে ওঠে, রাস্তাটা দেখাতে দেখাতে বলে, ‘এই যে রাস্তা দেখতেছেন, এই রাস্তা ধইরা সোজা চইলা যান। খানিক আগাইলেই দেইখবেন, কুনু বাড়িঘর নাই, খালি একখান স্কুল। দেইখলেই চিনবেন।’
‘এখন মাস্টাররা সবাই আছে?’
সূর্যের দিকে তাকিয়ে অনীল একটু বোঝার চেষ্টা করে, বলে, ‘এহন মনে কয় নাই। সমস্যা নাই, স্কুলের পিছনেই মাস্টার সাবের বাসা। ডাক দিলিই হব্যো।’
‘আপনি মাছ দিতে যাবেন না?’
‘মাছ?’—অনীল যেন বুঝতেই পারে না রিপন কী বলছে। কী বলবে কী বলতে করতে করতে রিপন বলেই ফেলে, ‘ওই যে খালই বোঝাই করে নিয়ে এলেন?’
‘ও,—ওই মাছ? কী যে কন না, এত অল্প মাছ! খসুল বাটা মাছের গল্প করতেছি, আর ছারেক দিমু এইসব এইটুক মাছ? যান, আপনে তাড়াতাড়ি ঘুইরা আসেন, আমি খানিক জিড়ায়া নেই। আপনেক নিয়া কইল করতোয়ায় যামু, খসুল বাটা ধরমু, রাতে রান্ধনবান্ধন
করমু।’
বলে অনীল বসে পড়ে গলুইয়ের ওপরে।
রিপনের গা ছমছম করে। কী ভীষণ নির্জন পথ! আর সত্যিই, ধারে কাছে কোনো বাড়িঘর নেই। জঙ্গলের ধার দিয়ে দু’তিনজন পাশাপাশি চলাফেরা করার মতো চাপা রাস্তা। আর ফসলের মাঠেও কোনো কিছু নেই। জঙ্গলে একটা বড় হলদে পাখি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু পাখির ডাক এখনো শুনতে পায়নি সে। হঠাৎ সামনে বিশাল দুই ডানার ছায়া পড়লে সে সভয়ে তাকায় আকাশের দিকে। একটা বিরাট শকুন উড়ে যাচ্ছে। হয়তো কোথাও গরু মারা গেছে। মরা গরুর ঘ্রাণের দিকে উড়ে চলেছে শকুন।
রাস্তা মনে হয় ফুরাতেই চায় না। রিপন যাচ্ছে তো, যাচ্ছেই। তা হলে অনীল যে বলল, খুব বেশি দূরে নয়! তা হলে সে কি ভুল রাস্তায় চলে এসেছে! নিশ্চয়ই না। সেরকম হতেই পারে না। তাকে এইভাবে গায়ের শক্তি খরচ করে জঙ্গলের কাছে এনে ফেলে দেবে—কী এত দায় পড়েছে ওই লোকটার।! তবে এখন শরীর ভার ভার লাগছে তার। কিছুই খাওয়া হয়নি সকাল থেকে, কথাটা মনে পড়ে এতক্ষণে। আর আরো মনে হয়, অজস্র লোকজন খচমচ করছে পুরো জঙ্গলজুড়ে। যদিও দুই চোখে তেমন কোনো আলামত খুঁজে পায় না সে।
তখনই মোড়টা একটু ঘুরতে না ঘুরতেই তার চোখে পড়ে, থরথরে প্রায় ভাঙাচোরা একটি বড় টিনের ঘর দাঁড়িয়ে আছে হয়তো-বা পোয়া মাইল দূরে। একটা বড় কড়িগাছ ছায়া দিচ্ছে সেটাকে। তার পায়ের গতি বেড়ে যায়, হৃদপিণ্ড ধুকপুক ধুকপুক করতে থাকে। টিনের ঘরটার সামনে গিয়ে সে উত্তেজনায় কোনো কথাই বলতে পারে না। তবে তার চোখ দুটো সেটাকে তন্নতন্ন করে খুঁজতে থাকে। না, কোনোখানে স্কুলের সাইনবোর্ড নেই। তবে টিনের ঘরের বেড়ার সঙ্গে ভূমি অফিসের আলকাতরায় লেখা ঘরবাড়ি নম্বর থেকে বোঝা যাচ্ছে, স্কুলই আসলে সেটা। যেন রূপকথার রাজ্যে এসে হাজির হয়েছে সে, তার ব্যাগের মধ্যে জিয়নকাঠি। সেটা বের করে স্পর্শ করলেই জেগে উঠবে পুরো বিদ্যালয়, শিশু-কিশোরদের কলতানে মুখরিত হয়ে উঠবে পুরো প্রাঙ্গণ।
টিনের ঘরের বারান্দায় উঠবে রিপন, তখনই ঘরের পেছনের শোলার বেড়ার আড়াল থেকে দীর্ঘদেহী এক মানুষ বেরিয়ে আসে। তার গায়ে কোনো জামা নেই, লুঙ্গি খাটো করে পরা, তবে মাথায় নারকেলের ছোবড়া দিয়ে বানানো একটা টুপি। চোখে কোনো মায়া-মমতা নেই, বরং এখনই জেগে উঠতে পারে ভয়ঙ্কর সহিংসতা। তবে সুন্দর করে হাসতে হাসতে সালাম দেয় সে। তারপর বলে, ‘চিনলাম না তো আপনেক। কইত্থেকে আসছেন?’
‘জ্বি, আমি—এই ঢাকা থেকে। আপনাদের স্কুলে একটা চাকরির বিজ্ঞাপন দেখলাম।’
লোকটার চোখেমুখে হিংস্রতা জেগে উঠতে গিয়েও মিলিয়ে যায়, ‘বুইঝলাম না।’
‘আপনাদের স্কুলে শুনলাম মাস্টার নেয়া হবে—’
‘আমাগারে ইসকুল? আমাগারে এহানে তো কুনু ইসকুল-টিসকুল নাই—’
‘এইটা স্কুল না? রামকান্দিপুর উচ্চ বিদ্যালয়? কমলকান্তি বাগচী হেডমাস্টার?’
‘কী কন না কন, কিছুই বুঝি না। রামকান্দিপুর
উচ্চ বিদ্যালয়? হোনেন, এইডো রসুলপুর গ্রাম। অ্যার ৫০ মাইলের মইধ্যে ওই নামে কুনু গাঁও নাই, স্কুলও নাই। বাগচী-মাগচীও নাই। দুই-এক ঘর যা আছিল, ভাইগা গ্যাছে। জুয়ান মিয়াগারে বিয়া দিবার পারে না, মিয়াগুলা ভাইগছে অ্যার-অর সাতে, হেরপর ভাইগছে বাপ-মায়েরা।’
একটু চুপ করে লোকটা আবারও বলে, ‘তে যান আপনে। আমার ঘরেও ঝি-বউ আছে, তারা পর্দা-ইজ্জত করে, আপনেগারে টাউনের মতো না। তারা এহন বাইর হব্যো, কাজকর্ম কইরব। এইখানে দাঁড়ায়া থাইকেন না। তাড়াতাড়ি যান—’
বলে লোকটা হাত উঁচালে এতক্ষণে রিপনের চোখে পড়ে, বড় একটা রামদাও রয়েছে তার হাতে। আতঙ্কে তার শরীর নীল হয়ে আছে। সে পিছু হটে শরীর ঘুরিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে হাঁটতে থাকে। জঙ্গলের পাশ দিয়ে, গাছগাছালির মধ্যে দিয়ে আর কতক্ষণে যে অনীলের নৌকার কাছে পৌঁছতে পারবে, কে জানে! নিশ্চয়ই অনীল তাকে নদী পার করে দেবে। কিন্তু কী আশ্চর্য, এবার সে দেখতে পায়, ঝোপজঙ্গল, গাছগাছালি, কোনো কিছু নেই—কোনো নদীও নেই কোনোখানে। সামনে বিস্তীর্ণ চরাচর, কোনো কোনো ক্ষেতে সামান্য ফসলের আভাস; কিন্তু মানুষজন, ঘরবাড়ি নেই। কোনো শ্যামলতা নেই, নির্জনতা নেই। তা হলে সে কি ভুল স্টেশনে নেমেছে? কিন্তু তা তো হওয়ার কথা নয়। আর কত লোকজনকে জিজ্ঞেস করে নিশ্চিত হয়েই না সে এখানে এলো। তারা সবাইও তা হলে ভুল বলল? এই যে অনীল তাকে নৌকায় করে নিয়ে এলো—সেই নদী নৌকাই বা কোথায় গেল?
রিপনের দম বন্ধ হয়ে আসে। ধুলো উড়ছে। হঠাৎ করেই রোদের আঁচ বাড়ছে যেন। কিন্তু সে হাঁটতে থাকে। স্কুলটা কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই আছে। সেখানে হয়তো নদী-নৌকা-অনীলও আছে। আর নিশ্চয়ই একটা চাকরিও আছে সহকারী শিক্ষক পদে। সে কোনো দিকে না তাকিয়ে, না থেমে হাঁটতেই থাকে একনাগাড়ে…

বাবার বিয়ে
সানজিদা আমীর ইনিসী
আমার মা মারা যাওয়ার পরের দিনে আমার দাদি বাবার জন্য মেয়ে দেখতে গেছিলেন। আমি থ্রিতে পড়ি তখন। মেয়ে দেখা, বিয়ে হওয়া এইসব বুঝি। মেয়ে দেখার কথা আমি আমার খালারে বললাম। খালা শুইনা কান্নাকাটি শুরু করল। আমারে বলল, “কপাল মন্দ। কী করবা মা!”
আমি কী করব জানতাম না। আসলে বাবা বিয়ে করলে কী-কী হবে তাও ঠিকঠাক বুঝতাম না। আত্মীয়স্বজন কারো সৎ মা নাই। তবে সৎ মা’রা কেমন হয় তা অনেক সিনেমায় দেখছি। সেইসবও সত্য বইলা বিশ্বাস করতে পারতাম না।
আমার মা যখন আমারে বকা দিত, তখন মা’রে বলতাম, “তোমারে বিক্রি কইরা বাজার দিয়া আরেকটা মা কিনা আনব।”
মা বলত, “তাইলেই সারছে! সেই ঘরে তোর আর ভাত খাওয়া লাগবে না।”
মা সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলত। আর সত্যি সত্যি, মা’র বলার ধরনে আমার ভয় লাগত। তখন ভাবতাম, মা সম্ভবত একজনই। ভাবতে ভাবতে বইতে পড়া পোয়েমের লাইনগুলি মাথায় ঘুরত।
“I know a face, a lovely face,
As full of beauty as of grace,
A face of pleasure, ever bright,
In utter darkness it gives us light
A face that is itself like joy,
To have seen it I’m a lucky boy
But I’ve a joy that have few others
This lovely woman is my mother.”
আমি বারবার বিড়বিড় করতাম “This lovely woman is my mother.”
আমি বাবাকে বললাম, দাদি মেয়ে দেখতে গেছিল। আর এও বললাম, আবার মেয়ে দেখতে গেলে আমি বাসা থিকা চইলা যাব। আর কখনো বাসায় ফিরব না। কথা বলতে বলতে আমি কাঁদতে ছিলাম। গলা বন্ধ হইয়া আসতেছিল। হাত-পা ঠান্ডা হইয়া যাইতেছিল। বইসা যেন ঠিকমতো বুঝায়ে বলতে পারতেছিলাম না। তাই দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে কথা বললাম। বাবা দাদিকে আমার সামনে মেয়ে দেখতে মানা করল। মানা করায় দাদি নিষ্ঠুরভাবে হাসলেন। তার হাসি দেইখা আমি আমার সামনে থাকা ফ্লোয়ার ভ্যাস ছুইড়া মারলাম মেঝেতে। সেইটা ভাইঙা কয়েক টুকরা হইল। বাবা কিছু বলল না। ঘর থিকা বের হইয়া গেল।
আমি দরজা আটকাইয়া অনেকক্ষণ কানলাম। মা’র ছবি বাইর কইরা দেখতে শুরু করলাম। সব ছবিতে মা হাসতেছে। আমার চোখের পানি অ্যালবামের ওপর টপাটপ পড়তে লাগল। মা’র মুখের ভঙ্গি তারপরেও একই রকম থাকতেছে। অথচ গতদিন, এই গতদিনও আমি কানলে মা’র চোখ ছলছল করত।
খালা বাসায় আইসা ডাকাডাকি করল। দরজা খুললাম। জড়ায়ে ধরলাম। কানলাম।
“খালার গা থিকা মা’র মতো গন্ধ আসে”—এইটা জানা থাকার জন্য কি-না জানি না, তবে মা’র গা’র গন্ধই পাইতেছিলাম। আমার ঘুম আসলো গন্ধে। আমি খালার কাঁধের ওপরই ঘুমায়ে পড়লাম।
দাদি এরপর সত্যিই মেয়ে দেখা বন্ধ রাখছিলেন। আমার সাথে আমার ফুফাত বোন থাকত। আমার চেয়ে সাত-আট বছরের বড়। মেট্রিক পরীক্ষায় ফেল করছে, আর পড়াশোনা করবে না, তাই সে আইসা থাকত। আমারে স্কুলে নিয়া যাইত, নিয়া আসত। ভাত খাওয়ায় দিত, গোসল করায় দিত, ঘুম পাড়ায় দিত। দাদি অন্য রুমে থাকতেন। সারাদিন তজবি জপতেন, আমারে দেখলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনলে আমার গা জ্বইলা যাইত। তখন চোখমুখ এক কইরা চুপচাপ বইসা থাকতাম।
মা মারা যাওয়ার এক সপ্তাহ পরে কোচিংয়ে যাওয়া শুরু করছিলাম। কোচিংয়ে নতুন এক ম্যাডাম আসছেন। একটু পর দেখলাম, সবাই তারে ঝর্ণা ম্যাডাম বইলা ডাকতেছে। আমার মা’র নামও ঝর্ণা। ম্যাডামের মুখের দিকে তাকাইতে আমার মন খারাপ হইল। ম্যাডাম সব জানতেন, এবং পুরো ক্লাস আমার পাশে বইসা রইলেন। মাঝেমধ্যে মাথায় হাত বুলাইতে ছিলেন। আমি চেষ্টা করতেছিলাম না কাঁদার জন্য। কিন্তু ম্যাডাম যখন বললেন, “থাক মা, মন খারাপ করে না”, তখন মুখ স্বাভাবিকের চেয়ে আরো নিচু কইরা ফেললাম। ক্লাসের সবাই তখন লেখা রাইখা আমার দিকে তাকায়ে আছে, কেউ কেউ কাঁদতেছে।
বাবা বিয়ে করল মা মারা যাওয়ার নয় মাস পর। এই নয় মাস প্রায় প্রতিদিন দাদির সাথে বিভিন্ন ব্যাপারে ঝামেলা হইত। বাবার চাকরি পটুয়াখালী, পটুয়াখালী থাকতে হয় তার। বৃহস্পতিবার রাত্তিরে বাসায় আসে, শুক্র শনিবার থাকে, রবিবার সকালে আবার চইলা যায়। দিনে আমি বাসায় থাকায় দাদি আমার ব্যাপারে বাবারে নালিশ করতে পারত না। তাই সে রাতে নালিশ করত। রাত তিনটা চারটার দিকে। আমি বাবা আসলে বাবার সাথে ঘুমাই। দাদি আর আপু অন্য রুমে। এক রাতে হঠাৎ ঘুম ভাইঙা গেল। লাইট জ্বলতেছে দেখলাম। দেখে চোখ বুজলাম। বুঝলাম দাদি বইসা আছে খাটের সামনে, সোফায়। বাবা তার পাশে। আমি রাগ দেখাই, ভাঙচুর করি, শুধু খালার কথা শুনি, তাদের কথা শুনি না—এসব বলতেছিলেন। বাবা শুইনা গেল। কিছু বলল না।
দাদির সাথে সমস্যা শুরু হইছিল মা’র তিনদিনের মিলাদের দিন। মিলাদের আগে দাদি মা’র ব্যাপারে ঠেস দিয়া কথা বলতেছিলেন। ঘর ভর্তি মানুষ ছিল সামনে। আমি শুনলাম শুধু। বাবাকে এই কথা পরে বলছি, সেও কিছু বলে নাই। বাবার কিছু না বলাতে আমার ভীষণ রাগ হইছে, এবং তার পর থিকা আমি দাদিকে একদম পছন্দ করি না।
আমি ফোরে ওঠার পর আপু আমাদের বাসা থিকা চইলা গেল। তার বিয়ে ঠিক হইছিল।
আপু ছাড়া বাসার কাজকর্ম করার কেউ নাই যেহেতু, বাসা ছাড়া হইল। মালপত্র পটুয়াখালী নিয়া গেল। আমি খালার কাছে রইলাম। বরিশালে। খালার ছেলেমেয়েদের বিয়ে হইয়া গেছে, সে একলা থাকে বিধায় ঝামেলা নাই।
খালা মাঝেমধ্যে আমারে বুঝাইত। বাবার বিয়ের ব্যাপারে। সে নিজেও মেয়ে দেখত। পছন্দ হইলে বাবারে জানাইত।
কিছুদিন পর একটা মেয়ে বাবার পছন্দ হইল। আমারে তখন সকাল-বিকাল নিয়ম কইরা বোঝানো হয়। দূরের আত্মীয়স্বজনরা ফোন কইরা বুঝান। আমি মাথা ঝাঁকাই, হু হু বলি। কান্নাকাটি করি। ছাদে গিয়া একলা বইসা থাকি। খালা আমারে ভূতের ভয় দেখাইত। ছাদে একলা থাকলে ভূত নাকি নিয়া যায়। আমি এইসব ভয়ের ধার ধারতাম না। আমি হুট কইরা ছোট থিকা বড় হয়ে গেছি। অনেক বড়, কখনো কখনো আমার আশপাশের সবার চেয়ে বড়।
কোচিং থিকা বাসায় ফেরার পথে আমি অনেক রাস্তা ঘুইরা হাঁইটা আসতাম। ব্যাগে রিকশাভাড়া জমা থাকত। জ্বর হইলে একলা ডাক্তার দেখাইতাম। ডাক্তার যখন দেখেন থ্রি কোয়ার্টার, ফতুয়া পরা, কাঁধে স্কুলব্যাগ নিয়া একটা মেয়ে একা আসছে তখন তার চোখেমুখে অবাক হওয়া ভাব থাকে। আমার তা ভালো লাগে। আমার মতো কেউ নাই আমার ক্লাসে। সবাই একলা রাস্তায় হাঁটতে ভয় পায়। রাস্তা পার হইতে ভয় পায়। আর একলা ডাক্তার দেখানো, হিহি, তা তো ভাবতেই পারে না। আমি ডায়েরি লিখতাম প্রতিদিন। কী-কী হইতেছে সব লিখে রাখতাম।
বাবার বিয়ের ব্যাপারে পাকা কথা হওয়ার পর একদিন আমাকে মেয়ের বাসায় নিয়া যাওয়া হইল। সাথে আমার খালা আর কাকা ছিলেন। আমি এই হবু মা’কে কী ডাকব বুঝতেছিলাম না। তার ওপর রাগ হইতেছে খানিক। কিন্তু সে দেখলাম খুব সহজ ব্যবহার করল। আমি হাত দিয়া খাইতে পারি না জানত। আমাকে খাওয়ায় দিলো। কথা বলল।
জিজ্ঞেস করলাম, “আপনার পড়াশোনা শেষ?”
“অনার্স শেষ। আরো অনেক আগে।”
“কী সাব্জেক্ট?”
“ফিজিক্স।”
“মানে অংক?”
“না। অংক না। তবে অংক আছে।”
কথা বইলা আমার ভাল্লাগল। বাসায় ফেরার পর আমার মতামত জানতে চাওয়া হইল। আমি সংক্ষেপে ‘হ্যাঁ’ বইলা প্রত্যেককে বিদায় দিলাম।
২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯।
আমার বয়স দশ।
খালার বাসায় লম্বা বারান্দা আছে। কোনায় একটা ইজিচেয়ার থাকে। আমি বইসা রইলাম সারা সকাল। মা কিভাবে চইলা গেল ভাবতেছি। গায়ে একটা হলুদ রঙের তাঁতের জামা ছিল। কুয়াকাটা থেকে কেনা। কতবার আমরা কুয়াকাটা গেছি, মা’র পাশে হাত ধইরা বালিতে হাঁইটা বেড়াইছি বা হাঁটছি ঝাউ গাছের পাশে। কতবার কত কম দুঃখে সারা দুপুর জড়ায়ে, পারলে কলিজার ভেতর ঢুইকা ঘুমাইছি। অথচ আজকের দিনটা কত দুঃখের, কত বিষণ্ণ।
২৫ ফেব্রুয়ারি বিডিআর বিদ্রোহ হইছে। নিউজ চ্যানেলে বলতেছে কী-কী যেন। বাবা টিভি দেখতেছে। পাশে ছোট কাকা। আমি ঘুইরা আসলাম তাদের সামনে থেকে। কারো সাথে কোনো কথা হয় নাই।
ছোট কাকা ঢাকা থিকা আসছে, বাবার বিয়ে উপলক্ষে। আজকে বাবার বিয়ে। সবাই প্রয়োজনের চেয়ে বেশি স্বাভাবিক। হবু মামা ইয়োলো একটা জামা পাঠাইছেন আমার জন্য। এইটা পইরা যাব, যেহেতু একদম নতুন।
খালার রুমে পালঙ্ক আছে। তার শ্বশুরের আমলের। পালঙ্কের মাথার কাছে বিশাল একটা মূর্তি। চোখ বন্ধ কইরা আছে। যেন সে পৃথিবীর ঘটমান কিছুই দেখতে চায় না; আমার মতো। আমি অনেকক্ষণ বইসা মূর্তিটা দেখি। দেখতে দেখতে আমার কাঁদতে ইচ্ছা করে। পাশের রাস্তায় জোরে গাড়ির হর্ণ পড়লে কাঁদার ইচ্ছা কমে।
দুপুরে বিয়ে হবে। আমরা একটার দিকে যাব। খুব অল্প মানুষ। আমার দাদাবাড়ির দিকের ছোট কাকা ছাড়া কেউ নাই। আর আমার আপন খালা, মামা, খালাত বোনেরা আছে।
কমিউনিটি সেন্টারে বিয়ে হয় নাই। মানুষজন কম যেহেতু, বাসাতেই বিয়ে হইছে। বাসায় আমার হবু মা’র মা, ভাই, ভাইয়ের বউ, বোন, বোনের জামাই আর তাদের বাচ্চাকাচ্চারা আছে। বিয়ে পড়ানোর পর দাদির সাথে বাবার ফোনে কথা হইছে। দাদি হয়তো এই বিয়েতে খুশি হন নাই। কারণ তার পছন্দে বিয়ে হয় নাই।
সিগনেচার-টিগনেচার হইয়া যাবার পর খালাত বোন আইসা তার চোখমুখ উজ্জ্বল কইরা আমাকে বলল, বিয়ে হয়ে গেছে।
সে সম্ভবত দেখতে চাইতেছিল আমি কী বলি বা কী করি।
আমি তারে বললাম, “এই বাসার বড় মামি মাটন চাপটা অনেক ভালো বানায়। আজকে খাইয়া দেইখো। আমি আগেও খাইছি।”
আপুর উৎসাহে ভাটা পড়ায় চেহারা বিমর্ষ হইল। সে চেয়ার টাইনা আমার থিকা দূরে গিয়া বসল।
আমার তখন আমার চারপাশের সবার মতো সবটা স্বাভাবিক মনে হইতেছে।
আমরা পটুয়াখালীর উদ্দেশ্যে রওনা দিছি বিকাল চারটায়। মাইক্রোর সামনে ড্রাইভারের পাশে বাবা বসছে। পেছনে আমি আর মা।
একটু পর মা’কে বললাম, আপনাকে সুন্দর লাগতেছে।
“থ্যাংক ইউ! মা’কে কেউ আপনি কইরা বলে নাকি! ‘তুমি’ বলবা।”
“আচ্ছা।”
মা’র খুব বেশি জার্নির অভ্যাস নাই। ভাঙা রাস্তার ঝাঁকাঝাঁকিতে বমি করল কয়েকবার। বমি করার আগে আমাকে বইলা নিলো, “তুমি সইরা বসো। আমার দিকে তাকায়ো না। বমি করতে দেখলে তোমারও বমি আসবে।”
আমি অন্যদিকে তাকায় থাকলাম। থাকতে থাকতে ঘুমায় গেলাম। পটুয়াখালী গিয়া যখন মা ডাক দিলো, তখন বুঝলাম ঘুমাইয়া গেছিলাম মা’র কাঁধের ওপর।
তারপর ঘুমজেগে অনেকদিন আর অনেকরাত পার করছি। এইসব দিনরাত্রিতে মা এক রাতে বলছিল, আমি বড় হইলে পরে অনেক গল্প হবে। এইটুক কথা বলতে মা কাঁদছিল সেই রাতে।
আমাদের সম্পর্ক যাই হোক না কেন, একটা কথা, একটা ডাক, আমাদের পিছু ডাকে সবসময়। আমি আমার আপন মা’র থিকা বেশি সময় ধরে তারে মা ডাকতেছি। মা’রেও আমার আগে কেউ মা ডাকে নাই। এই ব্যাপারগুলি আমাদের বাঁইধা রাখে। মাঝে ভালো দিন, কথা বন্ধের দিন, মুখে ভাত তুইলা খাওয়ায়ে দেওয়া দিন, হাসিঠাট্টার দিন, বিষণ্ণ দিন—কতদিন নদীর মতো বয়ে গেছে। আমি টের পাই না। দেখতে পাই ফ্রেমে থাকা আমাদের দিনগুলি; ভালো দিনগুলি নিয়ে যেসব বাঁধায়ে রাখছিলাম।








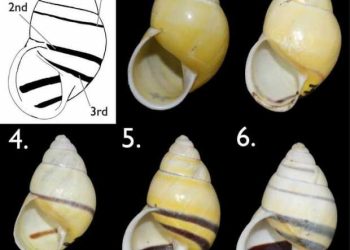









Discussion about this post